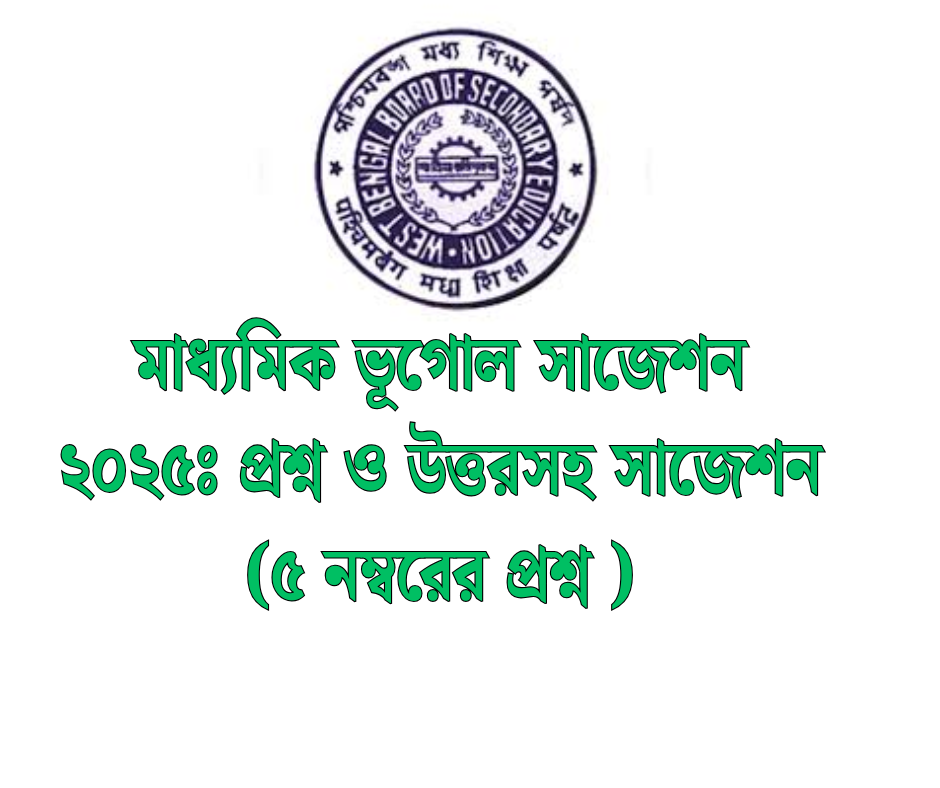মাধ্যমিক ভূগোল সাজেশন ২০২৫ঃ প্রশ্ন ও উত্তরসহ সাজেশন (৫ নম্বরের প্রশ্ন ):
ভারতে গম চাষের জন্য অনুকূল ভৌগোলি
ক পরিবেশ
গম ভারতের একটি প্রধান খাদ্যশস্য, যা মূলত রবি শস্য হিসেবে চাষ করা হয়। গম চাষের জন্য নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও পরিবেশগত শর্তাবলী প্রয়োজন, যা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান।
১. জলবায়ু
- তাপমাত্রা:
- গম চাষের জন্য বপনের সময় শীতল তাপমাত্রা (১০°-১৫°C) এবং ফসল কাটার সময় উষ্ণ তাপমাত্রা (২১°-২৬°C) প্রয়োজন।
- গমের বেড়ে ওঠার জন্য শীতল পরিবেশ এবং কেঁটেকাটার সময় উষ্ণ ও শুষ্ক পরিবেশ বিশেষ উপযোগী।
- আলো:
- পর্যাপ্ত সূর্যালোক ফসলের ভালো বৃদ্ধি নিশ্চিত করে।
২. বৃষ্টিপাত
- বছরে ৫০-৭৫ সেমি বৃষ্টিপাত গম চাষের জন্য আদর্শ।
- বেশি বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় না, তবে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো থাকতে হবে।
- কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে গম চাষ সম্ভব।
৩. মাটি
- গম চাষের জন্য উর্বর দোআঁশ মাটি অত্যন্ত উপযোগী।
- মাটির মধ্যে জৈব পদার্থ বেশি থাকা উচিত এবং জলধারণ ক্ষমতা ভালো হতে হবে।
- সঠিক পিএইচ স্তর ৬-৭ গম চাষের জন্য উপযুক্ত।
৪. অঞ্চল
ভারতে গম চাষের প্রধান অঞ্চলগুলি হলো:
- উত্তর ভারত: পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান।
- মধ্য ভারত: মধ্যপ্রদেশ।
- পশ্চিম ভারত: গুজরাট।
- পূর্ব ভারত: বিহার।
৫. সেচ ও প্রযুক্তি
- অনেক জায়গায় সেচের মাধ্যমে চাষ করা হয়, বিশেষ করে কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে।
- আধুনিক প্রযুক্তি এবং উচ্চফলনশীল বীজ গমের উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে।
গম চাষের জন্য শীতল ও শুষ্ক জলবায়ু, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, এবং উর্বর দোআঁশ মাটি প্রয়োজন। ভারতের উত্তর ও মধ্যভাগের সমভূমি অঞ্চল গম চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। সঠিক পরিবেশ ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে গম উৎপাদনে ভারত সাফল্য অর্জন করেছে।
ভারতে চা চাষের জন্য অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ
ভারত চা উৎপাদনে বিশ্বে অন্যতম প্রধান দেশ। বিশেষত উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু পাহাড়ি অঞ্চল চা চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। চা চাষের জন্য নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও পরিবেশগত শর্তাবলী প্রয়োজন।
১. জলবায়ু
- তাপমাত্রা:
- চা চাষের জন্য ২০°-৩০°C তাপমাত্রা আদর্শ।
- অত্যধিক ঠান্ডা বা গরম তাপমাত্রা চা গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত করে।
- বৃষ্টিপাত:
- বার্ষিক ১৫০-৩০০ সেমি বৃষ্টিপাত চা চাষের জন্য উপযুক্ত।
- নিয়মিত বৃষ্টিপাত চা গাছের পাতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।
২. উচ্চতা
- চা চাষ সাধারণত ৬০০-১৮০০ মিটার উচ্চতার পাহাড়ি এলাকায় ভালো হয়।
- উচ্চতার কারণে মাটির নিষ্কাশন ভালো হয় এবং ফসলের গুণগত মান উন্নত হয়।
৩. মাটি
- চা চাষের জন্য উর্বর, অ্যাসিডিক (পিএইচ ৪.৫-৫.৫) মাটি প্রয়োজন।
- পাহাড়ি এলাকায় লাল মাটি ও দোআঁশ মাটি চা চাষের জন্য উপযোগী।
- মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বেশি হওয়া জরুরি।
৪. সূর্যালোক
- ছায়াযুক্ত পরিবেশ চা চাষের জন্য উপযুক্ত।
- সকাল ও বিকালের হালকা সূর্যালোক চা গাছের বৃদ্ধি নিশ্চিত করে।
৫. অঞ্চল
ভারতে চা চাষের প্রধান অঞ্চলগুলি হলো:
- উত্তর-পূর্ব ভারত:
- আসাম (বিশ্বে অন্যতম বৃহত্তম চা উৎপাদক অঞ্চল)।
- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ (উচ্চমানের চা উৎপন্ন হয়)।
- দক্ষিণ ভারত:
- কেরালা (মুন্নার), তামিলনাড়ু (নীলগিরি)।
- অন্যান্য অঞ্চল:
- সিকিম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা।
৬. সেচ ও পরিচর্যা
- সঠিক সেচ ব্যবস্থা এবং জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে চা গাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।
- নিয়মিত পরিচর্যা, যেমন ছাঁটাই ও আগাছা পরিষ্কার করা, ফসলের গুণমান বজায় রাখে।সারসংক্ষেপ
চা চাষের জন্য নিয়মিত বৃষ্টিপাত, উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু, এবং উর্বর অ্যাসিডিক মাটি প্রয়োজন। আসাম, দার্জিলিং এবং নীলগিরির পাহাড়ি অঞ্চলগুলি চা চাষের জন্য বিশ্বখ্যাত। উন্নত প্রযুক্তি এবং সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে ভারত চা উৎপাদনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে।
ভারতে আখ চাষের জন্য অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ
আখ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল, যা ভারতীয় চিনি শিল্পের ভিত্তি। আখ চাষের জন্য নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত শর্ত প্রয়োজন।
১. জলবায়ু
- তাপমাত্রা:
- আখ চাষের জন্য ২১°-২৭°C তাপমাত্রা আদর্শ।
- উচ্চ তাপমাত্রা (৩০°C পর্যন্ত) ফটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, যা আখের বৃদ্ধি বাড়ায়।
- বৃষ্টিপাত:
- বার্ষিক ৭৫-১৫০ সেমি বৃষ্টিপাত উপযুক্ত।
- তবে চাষের সময় সেচের মাধ্যমে জল সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- আর্দ্রতা:
- মৃদু আর্দ্র পরিবেশ আখ চাষের জন্য উপযোগী।
২. মাটি
- ধরন:
- গভীর, উর্বর দোআঁশ মাটি আখ চাষের জন্য আদর্শ।
- মাটির পিএইচ মান ৬.৫-৭.৫ হলে ভালো ফলন হয়।
- জল ধারণ ক্ষমতা:
- মাটিতে উচ্চ জল ধারণ ক্ষমতা আখের বৃদ্ধি নিশ্চিত করে।
- সারের প্রয়োজন:
- জৈব সার এবং নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ সার ব্যবহার আখ চাষে উৎপাদন বাড়ায়।
৩. জল সরবরাহ
- বৃষ্টিপাত কম হলে কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।
- সেচ ব্যবস্থার উন্নতি আখের শিকড়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছে দেয়।
৪. অঞ্চল
ভারতে আখ চাষের প্রধান অঞ্চলগুলি হলো:
- উত্তর ভারত:
- উত্তর প্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, পাঞ্জাব (উচ্চ মানের আখ চাষ)।
- দক্ষিণ ভারত:
- তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ (উচ্চ ফলনের জন্য বিখ্যাত)।
- পশ্চিম ভারত:
- মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট (চিনি শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ)।
৫. আখ চাষের ঋতু
- আখ সাধারণত বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালীন ফসল।
- রোপণ সময়: ফেব্রুয়ারি-মার্চ (উত্তর ভারত), অক্টোবর-ডিসেম্বর (দক্ষিণ ভারত)।
৬. পরিচর্যা ও সেচ
- নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার এবং রোগ প্রতিরোধক স্প্রে ব্যবহার আখের গুণমান উন্নত করে।
- পর্যাপ্ত জল সরবরাহের জন্য ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার ব্যবহার চাষের ফলন বাড়ায়।
পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের কেন্দ্রভবনের কারণ
পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্প বা কাপড় বয়ন শিল্প একটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। এটি বিশেষত গুজরাট, মহারাষ্ট্র, এবং রাজস্থান অঞ্চলে বিকশিত হয়েছে। এই শিল্পের কেন্দ্রভবনের পেছনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে।
১. কাপাস বা তুলা উৎপাদন
- পশ্চিম ভারতে তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার উপযুক্ত মাপের কারণে এখানে তুলার উৎপাদন ব্যাপক। গুজরাট, রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্রের কিছু অঞ্চল তুলার উৎপাদনে শীর্ষ স্থান অধিকারী। তুলার প্রাচুর্য এই শিল্পের বিকাশে সহায়ক হয়েছে।
- গুজরাটে বিশেষত তুলা উৎপাদনের পরিমাণ উচ্চ, যা বয়ন শিল্পের জন্য কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করে।
২. বাণিজ্যিক যোগাযোগ
- পশ্চিম ভারতে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর যেমন কচ্ছ, মুম্বাই, এবং ধূয়ানী এর মাধ্যমে ভারতে এবং বিদেশে বাণিজ্যিক যোগাযোগ শক্তিশালী ছিল। বিশেষত, গুজরাটের বন্দরগুলো ছিল বিশ্বের সাথে সংযুক্ত, যা শিল্পের প্রসার ঘটাতে সহায়ক।
- এটি পশ্চিম ভারতের কার্পাস বয়ন শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির জন্য উন্মুক্ত করে দেয়, ফলে শিল্পের ব্যাপক উন্নতি ঘটে।
৩. কুম্ভকর্ণের শিল্প পরিবেশ
- পশ্চিম ভারতের শহরগুলোতে প্রচুর কুম্ভকার, শৈল্পিক পরিবেশ এবং কারিগরি দক্ষতা ছিল। এতে প্রচুর কারিগর ও বয়নশিল্পীরা তাদের দক্ষতা ও শিল্পের জন্য বিভিন্ন ডিজাইন তৈরি করতে পারতেন। এরা স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও নিজেদের নাম ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।
৪. মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের অভ্যন্তরীণ বাজার
- পশ্চিম ভারতে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য তুলা, সুতি কাপড়, এবং অন্যান্য বোনা পণ্য প্রচুর চাহিদা ছিল। এতে স্থানীয় শিল্পীরা উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন।
- স্থানীয় ব্যবসা এবং সাংস্কৃতিক চাহিদা এই শিল্পকে আরো শক্তিশালী করতে সহায়ক ছিল।
৫. সরকারি সহায়তা এবং নীতিগত সুবিধা
- ব্রিটিশ শাসনকালে পশ্চিম ভারতে শিল্পের জন্য সরকারী সহায়তা এবং নীতিগত সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। বিশেষ করে গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে আধুনিক কারখানার নির্মাণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, যা দেশীয় বয়ন শিল্পকে সমর্থন করে।
৬. তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা
- বয়ন শিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার ও নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন ও উন্নতি এই অঞ্চলে দ্রুত প্রসার লাভে সহায়ক ছিল। শীর্ষ মানের মেশিন ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন দ্রুততর হয়েছিল এবং পণ্যের গুণমান বৃদ্ধি পায়।
পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের কেন্দ্রভবন মূলত তুলার প্রাচুর্য, শক্তিশালী বাণিজ্যিক যোগাযোগ, অভ্যন্তরীণ চাহিদা, সরকারি সহায়তা এবং স্থানীয় শিল্পকৌশলির বিকাশের ফলস্বরূপ। এর মাধ্যমে এই অঞ্চলের শিল্পসমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হয়েছে।
পূর্ব ও মধ্য ভারতের লৌহ ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রভবনের কারণ
পূর্ব ও মধ্য ভারত, বিশেষত ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, এবং ওড়িশা অঞ্চলে লৌহ ইস্পাত শিল্পের বিকাশ হয়েছে। এই অঞ্চলের লৌহ ইস্পাত শিল্পের বিকাশের পেছনে বিভিন্ন ভূগোলিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। নিচে কিছু প্রধান কারণ আলোচনা করা হলো:
১. লৌহের প্রাচুর্য
- পূর্ব ও মধ্য ভারতের বিশেষ কিছু অঞ্চলে লৌহের খনি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং ওড়িশা অঞ্চলে লৌহের খনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর ও ওড়িশার রাউরকেলা এর মতো অঞ্চল লৌহের বিশাল মজুত রয়েছে, যা এই শিল্পের বিকাশে সহায়ক।
২. উচ্চমানের কাঁচামাল
- লৌহ ইস্পাত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যেমন কোকো (কোকো কাঠ বা কোকো পাথর) এবং চুনাপাথর এ অঞ্চলে পাওয়া যায়। এদের যোগান এই শিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- চুনাপাথর, কোকো এবং লৌহ উপাদানগুলো সহজেই এই অঞ্চলে পাওয়া যায়, যা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজ ও সাশ্রয়ী করেছে।
৩. বাণিজ্যিক সুবিধা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
- পূর্ব ও মধ্য ভারত এমন কিছু অঞ্চলে অবস্থিত, যেগুলো ভারতে বাণিজ্যিক যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলের শহরগুলি রেল, সড়ক এবং নদীপথে ভালোভাবে যুক্ত।
- জামশেদপুর এবং রাউরকেলা শহরগুলির কাছাকাছি বিশাল খনির মজুত এবং পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, এই শিল্পের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।
৪. সরকারি সহায়তা ও নীতিগত সুবিধা
- ব্রিটিশ শাসনকালে এবং স্বাধীনতার পরও ভারতের সরকার লৌহ ইস্পাত শিল্পে বিনিয়োগ এবং সহায়তা প্রদান করেছে। বিশেষ করে ভারতের প্রথম সরকারি লৌহ ইস্পাত প্রকল্প জামশেদপুর (টাটা স্টিল) ১৯০৭ সালে শুরু হয়েছিল, যা এই শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
- এই শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার বাণিজ্যিক সুবিধা এবং ট্যাক্স অবকাঠামোও প্রদান করেছে।
৫. শক্তিশালী শিল্পী ও কারিগরি দক্ষতা
- পূর্ব ও মধ্য ভারতের শিল্পী এবং কারিগররা লৌহ ইস্পাত উৎপাদনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা অর্জন করেছেন। এই অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই ধাতু গলানোর শিল্প ছিল, যা আধুনিক ইস্পাত শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে।
- এদের দক্ষতা লৌহের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে চমৎকার ইস্পাত উৎপাদনের জন্য সহায়ক।
৬. বিদ্যুৎ সরবরাহ ও আধুনিক প্রযুক্তি
- লৌহ ইস্পাত উৎপাদনের জন্য বিদ্যুৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহার অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো রয়েছে, যা এই শিল্পকে আরো বিকশিত করতে সহায়তা করেছে।
- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিল্প ব্যবস্থাপনার উন্নতি এই অঞ্চলে শিল্পের প্রসার ঘটিয়েছে।
পূর্ব ও মধ্য ভারতের লৌহ ইস্পাত শিল্পের বিকাশের পেছনে লৌহ খনি, কাঁচামালের প্রাচুর্য, শক্তিশালী বাণিজ্যিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরকারি সহায়তা, এবং কারিগরি দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই অঞ্চলের উপযুক্ত ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের প্রাচুর্য লৌহ ইস্পাত শিল্পের বিকাশে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে।
ভারতের নগরায়নের সমস্যাগুলি আলোচনা করোঃ
ভারতের নগরায়ন একটি দ্রুত পরিবর্তিত প্রক্রিয়া, যা সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, এই নগরায়নের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ জড়িত। এই সমস্যাগুলি ভারতের শহরগুলির উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মানের উপর প্রভাব ফেলছে। নিচে ভারতের নগরায়নের প্রধান সমস্যা গুলি আলোচনা করা হলো:
১. জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ
- ভারতের শহরগুলিতে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি একটি বড় সমস্যা। শহরগুলিতে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন সুবিধা, যেমন পানি, বিদ্যুৎ, সড়ক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি ব্যবস্থা চাপের মধ্যে পড়ে।
- এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা শহরের মৌলিক অবকাঠামোর ওপর ভারী চাপ সৃষ্টি করে এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে অপর্যাপ্ত পরিষেবা ব্যবস্থার সমস্যা তীব্র হয়ে ওঠে।
২. দুর্ভোগজনক ট্রাফিক ও যানজট
- শহরগুলিতে যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে যানজট এবং ট্রাফিক সমস্যায় বৃদ্ধি ঘটছে। রাস্তাগুলির অপ্রতুলতা, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার অভাব এবং যানবাহনের অতি সংখ্যা শহরের পরিবহন ব্যবস্থা অকার্যকর করে ফেলছে।
- যানজটের ফলে সময় এবং জ্বালানি খরচ বেড়ে যায়, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান কমিয়ে দেয়।
৩. বস্তিবাসী সমস্যা
- নগরায়নের ফলে অনেক মানুষ শহরে পাড়ি দেয়, কিন্তু তারা সকলেই শহরের উন্নত অঞ্চলগুলোতে বসবাস করতে পারে না। এর ফলে শহরের প্রান্তিক এলাকায় অস্থায়ী বস্তি গড়ে ওঠে, যেখানে বাসস্থান, পানির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি পরিষেবার অভাব থাকে।
- এই বস্তি অঞ্চলে অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং নাগরিক সুবিধার অভাব একদিকে মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যায় অবদান রাখছে, অন্যদিকে সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি করছে।
৪. পানির অভাব
- ভারতের অনেক শহরে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের অভাব রয়েছে। শহরের জনসংখ্যার চাপ এবং বৃষ্টিপাতের বৈষম্য এর জন্য দায়ী। কিছু শহর যেমন মুম্বাই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু ইত্যাদিতে পানির সঙ্কট একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- শহরগুলির বৃদ্ধির সাথে সাথে পানি সরবরাহের পরিমাণ অনেক কমে যাচ্ছে, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে।
৫. বায়ু দূষণ
- ভারতের শহরগুলোতে বায়ু দূষণ একটি গুরুতর সমস্যা। অধিক যানবাহন, শিল্পাঞ্চল, নির্মাণকাজ, এবং অন্যান্য কার্যক্রমের কারণে বায়ুর গুণমান ক্রমশ খারাপ হয়ে উঠছে।
- দিল্লি, কলকাতা, মুম্বাই, আহমেদাবাদসহ অনেক বড় শহরে বায়ু দূষণ জনগণের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকিতে ফেলছে, বিশেষত শ্বাসযন্ত্রের রোগ ও অ্যালার্জির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৬. কঠোর আবাসন সংকট
- ভারতের শহরগুলোতে আবাসন সংকটও একটি বড় সমস্যা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং অবকাঠামো উন্নয়নের অপ্রতুলতা কারণে শহরে যথাযথ আবাসন নির্মাণের জন্য ভূমির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে।
- বিশেষত শহরের মধ্যাঞ্চলে বাড়ি ভাড়া অত্যধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য বাসস্থান পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।
৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি
- শহরগুলির অপ্রতুল জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, ভূমিধস, খরা ইত্যাদি মোকাবিলা করার জন্য শহরগুলি প্রস্তুত নয়।
- এসব দুর্যোগ নগর জীবনের উন্নতি এবং নিরাপত্তা ব্যাহত করে।
৮. নগর পরিবেশ ও সবুজ অঞ্চল সংকট
- ভারতের অনেক শহরে সবুজ এলাকার অভাব দেখা যাচ্ছে। পার্ক, উদ্যান, বাগান এবং খেলার মাঠের অভাবে শহরের বাসিন্দাদের জন্য শ্বাস নিতে বা শখের সময় কাটানোর জন্য স্থান সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।
- বনভূমি, জলাশয় এবং সবুজ অঞ্চল দখল এবং নগরায়নের জন্য ধ্বংস হচ্ছে, যা পরিবেশগত ভারসাম্যকে হুমকির মুখে ফেলছে।
৯. অপরাধ বৃদ্ধি
- নগরায়ন বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে অপরাধের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা, শহরের খোলামেলা জায়গাগুলিতে অপরাধীদের আড়াল হওয়া এবং পুলিশের পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকার কারণে নগর অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে।
- চুরি, ডাকাতি, যৌন নিপীড়ন এবং অন্যান্য অপরাধের ঘটনা শহরের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ভারতের নগরায়নের দ্রুত বৃদ্ধি বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবহন সমস্যা, পানির অভাব, বস্তিবাসীর সংকট, বায়ু দূষণ, আবাসন সংকট, অপরাধ বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্যা ভারতের নগরায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে অন্যতম। এই সমস্যা সমাধানে সরকার এবং সমাজের একযোগে পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।